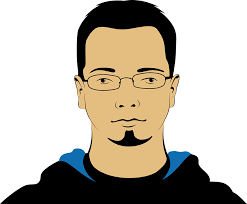

২৭ জানুয়ারি ২০২১ লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করেন নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। তার অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়।
হবংি২৪নফ.ঃা এর পাঠকদের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে প্রবন্ধটি এখানে প্রকাশ করা হলো।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে একটা কথা মনে হচ্ছে। তিনি শুধু বাংলার বন্ধু ছিলেন না, তাঁর ভূমিকা ছিল আরও অনেক বড়, এবং অতুলনীয়। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মহান রাজনৈতিক নায়ক, বাংলার সবচেয়ে সমাদৃত মানুষ, স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার। বাংলাদেশের জনজীবনে তাঁর প্রভাব আজও বিপুল। তাঁকে ‘বাংলাদেশের জনক’ বা বঙ্গবন্ধু বলাটা নিতান্তই কম বলা। তিনি যে এর চেয়ে বড় কোনও অভিধা চাননি, সেটা তাঁর সম্পর্কে আমাদের একটা সত্য জানায়— তিনি নাম কিনতে চাননি, মানুষ তাঁকে অন্তর থেকে ভালবাসত।
এক জন অতি চমৎকার মানুষ এবং এক মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর চিন্তাভাবনা কেন আজকের পক্ষেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে-বিষয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধুকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও দৃষ্টির সম্পদ কেউ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। তাঁর সেই চিন্তাভাবনা আজ আমাদের বড় রকমের সহায় হতে পারে। উপমহাদেশ আজ আদর্শগত বিভ্রান্তির শিকার হয়ে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে, এই দুর্দিনে পথনির্দেশ এবং প্রেরণার জন্য আমাদের বঙ্গবন্ধুর কাছে সাহায্য চাইবার যথেষ্ট কারণ আছে। শেখ মুজিবের চিন্তা এবং বিচার-বিশ্লেষণ যে সব দিক থেকে আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, এখানে তার কয়েকটির উল্লেখ করতে চাই।
প্রথমত, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা হিসেবে শেখ মুজিব ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে এই বিষয়ে সব দেশেরই শেখার আছে। বর্তমান ভারতের পক্ষে তো বটেই, বঙ্গবন্ধুর ধারণা ও চিন্তা উপমহাদেশের সব দেশের পক্ষেই শিক্ষণীয়। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে বাংলাদেশ অনেক উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তিনি কেমন বাংলাদেশ চান, বঙ্গবন্ধু সে কথা পরিষ্কার করে বলেছিলেন। তাই আমরা খুব সহজেই ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে তাঁর অবস্থানটা বুঝে নিতে পারি।
এ-কথা জোর দিয়ে বলব যে, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং লোকেদের স্বক্ষমতা-র মধ্যে যোগসূত্রটি শেখ মুজিবকে প্রভূত অনুপ্রেরণা দিত (স্বক্ষমতা শব্দটি ইংরাজি ‘ফ্রিডম’-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করছি)। ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতার যে ধারণা বহুলপ্রচলিত, তাতে ধর্মের প্রতি সাধারণ ভাবে একটা বিরূপতা পোষণ করা হয়ে থাকে। এই ধারায় মনে করা হয়, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কখনও কোনও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মকে উৎসাহ দেবে না, বা সাহায্য করবে না।
আমেরিকায় মাঝেমধ্যে এই গোত্রের ধর্মনিরপেক্ষতা অনুশীলনের চেষ্টা হয়েছে, তবে সে দেশের বেশির ভাগ মানুষের মনে ঈশ্বর এবং খ্রিস্টধর্মের আসন এতটাই পাকা যে, সেই উদ্যোগ কখনওই খুব একটা এগোতে পারেনি। যে কোনও রকমের ধর্মীয় আচার থেকে রাষ্ট্রকে দূরে রাখতে ফরাসিরা তুলনায় অনেক বেশি সফল, কিন্তু ধর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলার চরম ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্য সে দেশেও দূরেই থেকে গেছে। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা পরিষ্কার: ধর্মনিরপেক্ষতার এমন কোনও অর্থ কখনওই তাঁর চিন্তায় স্থান পায়নি, যা মানুষের ধর্মাচরণের স্বক্ষমতাকে অস্বীকার করবে। যাঁদের ধর্মবিশ্বাস গভীর, তাঁদের কাছে এই স্বক্ষমতা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।
এই কারণেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্ম-বিরোধিতা হিসেবে দেখবার চিন্তাধারাকে মুজিবুর রহমান বিশেষ মূল্য দেননি। ধর্মীয় আচারকে এড়িয়ে চলার বা ‘ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার’ তাগিদে ধর্মাচরণের স্বক্ষমতাকে অস্বীকার করার কোনও প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অনুসরণ অর্থে শেখ মুজিব ঠিক কী বুঝতে চেয়েছিলেন? ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকায় বাংলাদেশের আইনসভায় সে-দিনের নবীন ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সংবিধান গ্রহণের সময় তিনি বলেছিলেন:
“আমরা ধর্মাচরণ বন্ধ করব না… মুসলমানরা তাঁদের ধর্ম পালন করবেন… হিন্দুরা তাঁদের ধর্ম পালন করবেন… বৌদ্ধরা তাঁদের ধর্ম পালন করবেন… খ্রিস্টানরা তাঁদের ধর্ম পালন করবেন… আমাদের আপত্তি শুধু ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারে।”
ধর্মাচরণের স্বক্ষমতাকে এখানে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যাকে বর্জন করতে বলা হচ্ছে তা হল ধর্মকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা, তাকে রাজনীতির উপকরণ বানানো। এটি এক ধরনের স্বক্ষমতা-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা রাষ্ট্রকে লোকের নিজের নিজের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করে। বস্তুত, আমরা আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে বলতে পারি: মানুষকে স্ব-ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মাচরণের স্বক্ষমতা ভোগ করতে সাহায্য করা উচিত, কেউ যাতে কারও ধর্মাচরণে বাধা দিতে না পারে সে জন্য যা করণীয় করা উচিত। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের ভূমিকা আছে।
দুঃখের কথা হল, ইদানীং ভারতে এই নীতি ও আদর্শ বেশ বড় রকমের বাধার সম্মুখীন। বিভিন্ন ধর্মের প্রতি আচরণে প্রায়শই বৈষম্য করা হচ্ছে, হিন্দুত্বের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এমনকি নাগরিকত্বের প্রশ্নেও, তাদের পছন্দসই ধর্মগোষ্ঠীর মানুষকে বিশেষ সুযোগসুবিধা দিচ্ছে।
ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিশেষ সম্প্রদায়ের (যেমন, মুসলমান, বা নিম্নবর্ণের হিন্দু বা আদিবাসী) বিশেষ বিশেষ খাদ্য (যেমন, গোমাংস) নিষিদ্ধ করার ফরমান জারি হয়েছে, যে হেতু এ ব্যাপারে অন্য ধর্মের কিছু লোকের (বিশেষত গোঁড়া হিন্দুদের) আপত্তি আছে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বিবাহে নিয়ন্ত্রণ, কখনও বা নিষেধাজ্ঞা, জারি করা হচ্ছে— সংশ্লিষ্ট ধর্মমতে এমন বিবাহ নিয়ে কোনও সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও।
এবং, বিবাহের উদ্দেশ্যে জোর করে মেয়েদের ধর্মান্তর করানোর নানা কাহিনি প্রচার করা হচ্ছে, অথচ বিভিন্ন মামলার সূত্রে প্রায়শই ধরা পড়েছে যে এ-সব গল্প একেবারেই ভুয়ো।
ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে মোগল সম্রাট আকবর যথেষ্ট পরিষ্কার ধারণা নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, লোকে নিজে যে ভাবে যে ধর্ম পালন করতে চায় তাতে কোনও বাধা দেওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্র এই স্বক্ষমতা রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে, কিন্তু কোনও ধর্মকে বিশেষ সুবিধা দেবে না।
দেখা যাচ্ছে, এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার দু’টি নীতি কাজ করছে: (১) বিভিন্ন ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণে কোনও ‘অ-সমতা’ থাকবে না (আকবর এই ব্যাপারটিতে জোর দিয়েছিলেন) এবং (২) ‘ধর্মকে রাজনৈতিক কারণে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে না’ (বঙ্গবন্ধুর কাছে যা গুরুত্ব পেয়েছিল)। এ-দুটো ঠিক এক নয়।
কিন্তু দুই আদর্শের যে কোনওটি লঙ্ঘিত হলে লোকের ধর্মীয় স্বক্ষমতা একই ধরনের বাধার সম্মুখীন হবে, কারণ সাধারণত এক ধর্মের তুলনায় অন্য ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণেই ধর্মীয় স্বক্ষমতা খর্ব করা হয়ে থাকে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের ঘটনাগুলিতেও এর অনেক প্রমাণ মেলে।
শেখ মুজিব, এবং আকবর, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি যে ভাবে পরিষ্কার করেছিলেন, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া কেবল ভারতে নয়, অনেক দেশেই গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকায় বা ইউরোপে অনুরূপ নানা বৈষম্য, যেমন জাতিগত বা নৃগোষ্ঠীগত অসাম্য বিষয়ক রাজনৈতিক আলোচনাতেও এই ধারণা প্রাসঙ্গিক। উপমহাদেশে, পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার মতো দেশে সমকালীন নানা বিতর্কে ও বিক্ষোভে জড়িত বিভিন্ন প্রশ্নেও তা আলো ফেলতে পারে।
ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখলে বোঝা যায়, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিটা বিশেষ উদ্বেগজনক, কারণ অনেকগুলো দশক ধরে এ-দেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের চর্চা এই সে-দিন অবধি অনেক দেশের তুলনায় বেশ সবল ছিল। দেশের কিছু রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে আগামী এপ্রিল-মে মাসে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা।
ধর্মনিরপেক্ষতার মূল প্রশ্নগুলি নিয়ে, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু তার যে মৌলিক শর্তাবলির কথা বলেছিলেন সেই সব বিষয়ে এখন বড় রকমের আলোচনার প্রয়োজন। তার কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ মেনে চলার— এবং লঙ্ঘন করার— ব্যাপারে নানা রাজনৈতিক দলের আচরণ কিছু রাজ্যের ভোটের লড়াইয়ে বিশেষ প্রাসঙ্গিক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করার যে নীতিতে বঙ্গবন্ধু জোর দিয়েছিলেন, এই প্রসঙ্গে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ— শুধু বাংলা নয়, গোটা বিশ্বের পক্ষেই। বঙ্গবন্ধুকে তাই ‘বিশ্ববন্ধু’ হিসেবেও আমরা সম্মান জানাতে পারি।
শেখ মুজিব যে কেবল ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্বক্ষমতা প্রসারের জায়গা থেকে দেখেছিলেন তা নয়, সাধারণ ভাবেই স্বক্ষমতার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। বস্তুত, যে মাতৃভাষার দাবি আদায়ের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, স্বক্ষমতার প্রশ্নটি ছিল তার একেবারে কেন্দ্রে, মাতৃভাষা ব্যবহারের স্বক্ষমতার দাবির সঙ্গে বাঙালি জাতির ধারণাটিও ওই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।
এটা একটা প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিষয়েই, যেমন শ্রীলঙ্কায় সিংহলি ও তামিল ভাষার আপেক্ষিক গুরুত্বের ব্যাপারে। শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক নেতারা শেখ মুজিবের ভাষা বিষয়ক চিন্তাভাবনার প্রতি মনোযোগী হলে এবং মাতৃভাষার প্রতি লোকের মমতা ও শ্রদ্ধাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন স্বীকার করলে হয়তো সে দেশের যুদ্ধ এবং বিপুল রক্তক্ষয় অনেকটাই কম হতে পারত। ভাষা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সামাজিক বিশ্লেষণের যে প্রজ্ঞা, তার গুরুত্ব বাংলার সীমা ছাড়িয়ে বহু দূরে প্রসারিত।
ভারতের স্বাধীনতার অল্প কালের মধ্যেই সমস্ত প্রধান ভাষাকে দেশের সংবিধানে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার ফলে অনেক গুরুতর সমস্যা এড়ানো গিয়েছিল। সেটা শেখ মুজিব স্বদেশের বড় নেতা হয়ে ওঠার অনেক আগেকার কথা বটে, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার কিছু কিছু দিক ভারতের এই ভাষা-নীতির ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক।
জাতীয় ভাষার সাংবিধানিক মর্যাদা প্রধান ভাষাগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছিল বটে, কিন্তু হিন্দি ও ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহারের ফলে অন্য প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে তাদের একটা অসমতা তৈরি হয়, যার কিছুটা হয়তো অনিবার্য ছিল। যাঁদের মাতৃভাষা হিন্দি (বা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ইংরেজি), অন্যদের তুলনায় তাঁরা কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়ে যান। সরকারি কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সমতা বিধানের প্রশ্নটি বাস্তবের সাপেক্ষেই বিচার করতে হবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অসাম্যের ব্যাপারটাকে হয়তো আরও বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখার দরকার আছে।
এ-সমস্যাটা হয়তো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও কিছুটা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রশ্নটি আরও অনেক বড়। সেখানকার ভাষাগুলি সংস্কৃত থেকে আসেনি, এসেছে প্রধানত প্রাচীন তামিল থেকে। একটু অতিসরলীকরণের ঝুঁকি নিয়ে বলা যায়, শেখ মুজিব বরাবর স্বক্ষমতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং মর্যাদা, স্বীকৃতি, সরকারি কাজে বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের মতো বিষয়গুলিকে এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেই দেখা দরকার।
শেষ করার আগে সমতার প্রসার বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনা নিয়ে দু’একটা কথা বলা যেতে পারে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অবিভক্ত পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার ও স্বাধীনতার যে দাবি তোলে, তার পিছনে বড় ভূমিকা নিয়েছিল সমতা প্রসারের প্রশ্ন। ১৯৭০-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনের প্রচারপর্বে বিভিন্ন ভাষণে দেশের নানা বর্গের মানুষের সামনে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতার প্রশ্নটিকে পেশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমতার প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিয়ে তার ভিত্তিতে তিনি এই নীতির উপর জোর দেন যে, ‘সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের অন্য সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার এবং সুযোগ ভোগ করার স্বত্ব থাকা চাই।’
পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু সমতার আদর্শ থেকে সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকারের এই দাবি ঘোষণা আওয়ামী লীগের সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, তার একটা বড় কারণ ছিল বঙ্গবন্ধুর নীতিনিষ্ঠ সওয়াল (জাতীয় আইনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়ী হয়েছিল আওয়ামী লীগ)। ন্যায্য লক্ষ্য পূরণের জন্য সুষ্ঠু যুক্তিপ্রয়োগ যে কার্যকর হতে পারে, বঙ্গবন্ধুর জীবনের ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নানা কাহিনিতে তার প্রমাণ আছে। সেটাও কম শিক্ষণীয় নয়।
ইতিহাসের একটি ব্যাপার উল্লেখ করে কথা শেষ করব। বঙ্গবন্ধু তাঁর নৈতিক আদর্শগুলির সঙ্গে বাংলার পুরনো মূল্যবোধের সম্পর্কের কথা অনেক বারই বলেছেন। সমতার প্রতি তাঁর আগ্রহের তেমন কোনও ঐতিহাসিক যোগসূত্র আছে কি? উত্তরে বলা যায়: হ্যাঁ, আছে। যেমন, অনেক কাল আগে থেকেই বাংলার সমাজসচেতন কবি ও চারণদের কবিতায় সমতার ধারণাটি গুরুত্ব পেয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের মতো বিদ্রোহী কবির লেখায় তো বটেই, একেবারে প্রথম যুগের বাংলা কবিতাতেও এমন সূত্রের সন্ধান আছে।
একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। দশম শতাব্দীর বাংলা ভাষায় লেখা চর্যাপদ-এ আমরা পড়ি, বৌদ্ধ কবি সিদ্ধাচার্য ভুসুকু তাঁর নদীপথে পূর্ববঙ্গে যাওয়ার কথা লিখছেন। পূর্বগামী সেই যাত্রাপথে তাঁর নানা অভিজ্ঞতা হয়, যেমন, জলদস্যুরা তাঁর সব কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যায় (ভুসুকু বলেন তিনি সে জন্য বিলাপ করবেন না), আবার সমাজের সবচেয়ে নিম্নবর্গের এক জন নারীর— এক চণ্ডালিকার— সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় (তিনি এই বিবাহে পুলকিত হন)। এবং, সিদ্ধাচার্য— আজ থেকে হাজার বছর আগে— সমতার বন্দনা করে লেখেন:
বাজ ণাব পাড়ী পঁউয়া খালেঁ বাহিউ।
অদঅ বঙ্গালে দেশ লুড়ি।।
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।।
(পেড়ে এনে বজ্রনাও পদ্মখালে বাওয়া/ লুট করে নিল দেশ অদ্বয় বঙ্গাল/ আজকে ভুসুকু হল (জাতিতে) বঙ্গালি/ চণ্ডালীকে (ভুসুকুর) পতœীরূপে পাওয়া।)
দেখা যাচ্ছে, হাজার বছর আগেও এক জন ‘যথার্থ বাঙালি’র মূল্যবোধগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হত। মনে রাখা দরকার, এই মূল্যবোধগুলোর অন্যতম ছিল সমতার সমাদর। এখানে ইতিহাসের ধারাবাহিকতার কিছু প্রমাণ আছে। সিদ্ধাচার্য যাঁদের ‘যথার্থ বাঙালি’ বলেছেন, তাঁরা যে আদর্শগুলির সমাদর করতেন, সেই ঐতিহ্যবাহিত মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের সংযোগ সাধন করা যায়, যে ধর্মনিরপেক্ষতা আজ আমাদের পক্ষে বিশেষ দরকারি। এই বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর উজ্জ্বল চিন্তাভাবনা আমাদের প্রেরণা দিতে পারে।